হাকিকুল ইসলাম খোকন//
৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ ইং জেনারেল এমএজি ওসমানি পি ,এস ,সি(অবসর প্রাপ্ত) কে আহবায়ক করে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ সমর্থিত জাতীয় জনতা পার্টি গঠন করা হয়েছিল।যার বর্তমান নাম বাংলাদেশ জনতা পার্টি (বিজেপি-ওসমানী)।
জাতীয় সম্মিলিত ফোরাম (জেএসএফ ) “র সংগঠক হাজী আনোয়ার হোসেন লিটন এক বিবৃতিতে উইকিপিডিয়া থেকে বিবৃত করে বলেছে , ১৯৩৯ সালে ভূগোলে এম এ প্রথম পর্ব পড়ার সময় বৃটিশ-ভারতীয় সেনা বাহিনীতে যোগদান করেন। ছাত্র হিসাবে সব সময়ই ওসমানী অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি দক্ষতার পরিচয় দেন। ন্যায়পরায়ণতা, শৃংখলা এবং কর্তব্যপরায়ণতা তার চারিত্রিক গুণাবলী বিশেষভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছাত্রজীবনেই ওসমানীর মধ্যে ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের ছাপ ফুটে ওঠে। যোগ্যতার স্বীকৃতি হিসেবে তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউ.ও.টি.সি’র (ইউনিভার্সি্িট অফিসার্স ট্রেনিং কোর) সার্জেন্ট নিযুক্ত হন। ওসমানী ১৯৩৯ সালে জুলাই মাসে বৃটিশ-ভারতীয় সেনা বাহিনীতে যোগদান করেন। তিনি ১৯৪০ সালে ৫ অক্টোবর দেরাদূন সামরিক একাডেমি হতে সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে আর্মির কিং কমিশন প্রাপ্ত হন। ১৯৪১ সালে ১৭ই ফেব্রুয়ারি ক্যাপ্টেন পদে পদোন্নতি লাভ করেন এবং যোগ্যতার বলে তিনি ১৯৪২ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে ব্রিটিশ আর্মির সর্ব কনিষ্ট মেজর হন। মাত্র ২৩ বছর বয়সে একটি ব্যাটোলিয়ানের অধিনায়ক হয়ে নজীরবিহীন রেকর্ড সৃষ্টি করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত বার্মার রণাঙ্গনে স্বতন্ত্র যান্ত্রিক পরিবহনে এক বিশাল বাহিনীর অধিনায়কত্ব দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৫ সালে ওসমানী তার পিতার ইচ্ছা পূরণে আই.সি.এস পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে উত্তীর্ণ হন। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। ১৯৪৭ সালে বৃটেন ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা প্রদান করলে, একই সালে ১৪ ও ১৫ই আগস্ট পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি স্বতন্ত্র দেশ বিশ্ব মানচিত্রে আবির্ভূত হয়। ১৯৪৭ সালে ৭ অক্টোবর লেফটেন্যান্ট কর্নেল হিসেবে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং ১৯৪৮ সালে পশ্চিম পাকিস্তানে কোয়েটা স্টাফ কলেজ থেকে পি.এস.সি ডিগ্রী লাভ করেন। ওসমানীকে ১৯৫৫ সালে ১২ ডিসেম্বর পাকিস্তানের সেনা সদর অপারেশন পরিদপ্তরে জেনারেল স্টাফ অফিসার নিয়োগ করা হয়। এখানে তাকে ১৯৫৬ সালে ১৬ মে মাসে কর্ণেল পদে পদোন্নতি প্রদান করে ডেপুটি ডাইরেক্টর এর দায়িত্বে নিয়োগ করা হয়। এ-সময় আন্তর্জাতিক সংস্থা সিয়াটো ও সেন্টোতে ওসমানী পাকিস্তান বাহিনীর প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে ওসমানীর দক্ষতার সংগে ডেপুটি ডাইরেক্টর অব মিলিটারি অপারেশনের দায়িত্ব পালন করেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্ণেল পদে কর্মরত থাকাকালীন ওসমানী একজন স্বাধীন চেতা বাঙ্গালী সেনা কর্মকর্তা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ১৯৬৭ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি কর্নেল পদে থাকা অবস্থায় অবসরে যান ওসমানী।
২৫ মার্চের কালরাত্রি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হঠাৎ আক্রমণের আগেই রাজনীতিবিদরা দেশ ছেড়ে কলকাতায় গিয়েছিলেন। পুরো জাতি যখন নেতৃত্বহীন ও দিশেহারা, ঠিক সে সময়ে দুঃসাহসী এক সেনানায়কের আবির্ভাব ঘটে পাল্টা আক্রমণে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য। তিনি জেনারেল মুহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানী। বাংলাদেশের ইতিহাসে তিনি কিংবদন্তির মহানায়ক। আজ মুক্তিযুদ্ধের সেই সর্বাধিনায়কের ৪০ তম মৃত্যুবার্ষিকী।
৩ নভেম্বর রাতে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করে ঘাতকরা। ৪ নভেম্বর এই খবর ছড়িয়ে পড়ে। মূলত এটা জানার পর ওসমানী রাষ্ট্রপতির প্রতিরক্ষা উপদেষ্টার পদ থেকে পদত্যাগ করেন। এ নিয়ে লে. কর্নেল এমএ হামিদ লিখেছেন, ‘গভীর রাত। ওসমানী বারান্দায় (বঙ্গভবনের) এসে দাঁড়ালেন। তাঁর বাসায় যাওয়ার গাড়ি নাই। বললেন, ‘এখন আমি আর ডিফেন্স উপদেষ্টা নই। সুতরাং সরকারি গাড়ি ব্যবহার করবো না।’ পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কর্নেল মালেক এগিয়ে এসে বললেন, ‘স্যার, আপনি আমার গাড়িতে আসুন। আমি আপনাকে বাসায় পৌঁছে দেবো।’ ওসমানী তাঁর (মালেকের) গাড়িতে করেই গভীর রাতে বাসায় ফিরলেন।’
জাতীয় সম্মিলিত ফোরাম (জেএসএফ ) “সংগঠক হাজী আনোয়ার হোসেন লিটন বিবৃতিতে আরোও বলেছে ন,১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল বঙ্গবীর ওসমানীকে মন্ত্রিসভায় জাহাজ চলাচল, অভ্যন্তরীণ নৌ ও বিমান মন্ত্রী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেন। ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৯৪ শতাংশ ভোট পেয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং আগের মন্ত্রণালয়সহ ডাক, তার ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বও পালন করেন। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংসদীয় গণতন্ত্র বিলুপ্ত করে বাকশাল কায়েম করলে এর তীব্র প্রতিবাদ করে ওসমানী সংসদ সদস্য পদ, মন্ত্রিত্ব ও আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৭৬ সালে ৫ সেপ্টেম্বর তার স্বপ্ন ‘সংসদীয় গণতন্ত্র’ পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি ‘জাতীয় জনতা পার্টি’ নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন এবং ‘গণনীতির রূপরেখা’ নামে একটি বই রচনা করেন। ১৯৭৮ ও ১৯৮১ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পেছনে ওসমানীর অবদান অসামান্য।
জেনারেল ওসমানী তার সারা জীবন কাটিয়েছেন এ দেশের মাটি ও মানুষের মুক্তির জন্য, উন্নতির জন্য ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। উৎসর্গ করেছেন তার জীবন-যৌবন, সহায়-সম্পত্তি ও সব কিছু। অবহেলিত বাঙালি মুসলমানদের ব্রিটিশ-ভারতীয় সেনাবাহিনীতে প্রবেশের জন্য তিনি সব প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিলেন এবং এর সফলতাও অর্জন করেছেন ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট প্রতিষ্ঠা করার পথকে উন্মুক্ত করে এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে ১৯৪৮ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি প্রথম ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট প্রতিষ্ঠার পর একে একে এ রেজিমেন্ট সমৃদ্ধ হতে থাকে, যা স্বাধীনতা যুদ্ধে নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে। অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে তিনি কখনো পিছু হটেননি। বাংলাদেশ পৃথিবীর বুকে যত দিন টিকে থাকবে তত দিন বঙ্গবীর জেনারেল ওসমানী বেঁচে থাকবেন এ দেশের মাটি ও মানুষের মনের মণিকোঠায় মুক্তির সুউজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হিসেবে।
১৯৭১ সালের ২৬শে ডিসেম্বর তাকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জেনারেল পদমর্যাদা (অক্রিয়) প্রদান করা হয় এবং তিনি নব দেশের প্রথম সশস্ত্র বাহিনী প্রধান হিসেবে নিযুক্তি পান। ১৯৭২ সালের ১২ এপ্রিল তিনি তার এ দায়িত্ব থেকে অবসর নেন, মন্ত্রিসভায় যোগ দেন অভ্যন্তরীণ নৌ যোগাযোগ, জাহাজ ও বিমান মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে। ১৯৭৩ সালের মার্চে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়৷ ঐ নির্বাচনে ওসমানী তার নিজের এলাকা থেকে অংশ নেন এবং নির্বাচনে অভাবনীয় সাফল্য লাভ করেন৷ ১৯৭৩ এর নির্বাচনে ওসমানী ৯৪ শতাংশ ভোটে বিজয়ী হয়েছিলেন৷ ডাক, তার, টেলিযোগাযোগ, অভ্যন্তরীণ নৌ যোগাযোগ, জাহাজ ও বিমান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নেন। ১৯৭৪ সালের মে মাসে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৭৫ সালে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে একদলীয় বাকশাল ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হলে তিনি সংসদ সদস্যপদ এবং আওয়ামী লীগের সদস্যপদ ত্যাগ করেন।
ওসমানীর জন্ম ১৯১৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর । তার পৈত্রিক বাড়ি সিলেট জেলার বালাগঞ্জ থানার (অধুনা ওসমানী নগর উপজেলা) দয়ামীরে। তার পিতা খান বাহাদুর মফিজুর রহমান, মাতা জোবেদা খাতুন। খান বাহাদুর মফিজুর রহমানের দুই ছেলে ও এক মেয়ের মধ্যে সবার ছোট ছেলে ওসমানী। ওসমানীর জন্মের প্রাক্কালে ১৯১৮ সালে খান বাহাদুর মফিজুর রহমান তৎকালীন আসামের সুনামগঞ্জ সদর মহকুমায় সাব ডিভিশনাল অফিসার হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন ৷ তাদের বসবাস ছিল সুনামগঞ্জ সদরেই। এখানেই জন্ম হয় ওসমানীর।
বীর সিপাহসালার শুধু মুক্তিযুদ্ধই নয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ১৯৪৭ ও ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তানের দু’টি যুদ্ধেও বীরত্বের সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন।
১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের কোয়েটা স্টাফ কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েশন লাভ করেন জে. ওসমানী। ১৯৪৯ সালে চিফ অব জেনারেল স্টাফের ডেপুটি নিযুক্ত হন। ১৯৫০ সালে যশোর সেনানিবাসে ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রথম ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক নিযুক্ত হন এবং চট্টগ্রাম সেনানিবাসে ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার প্রতিষ্ঠা ও এর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ববাংলার আরো কয়েকটি আঞ্চলিক স্টেশনের দায়িত্বও তিনি সফলতার সাথে পালন করেন? পরে ১৪তম পাঞ্জাব রেজিমেন্টের নবম ব্যাটালিয়নের রাইফেলস কোম্পানির পরিচালক, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের (ইপিআর) অতিরিক্ত কমান্ড্যান্টের দায়িত্ব পালন করেন।
তথ্য সূত্র: জে এন দীক্ষিত- লিবারেশন অ্যান্ড বিয়ন্ড: ইন্দো-বাংলাদেশ রিলেশন্স, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৯, পৃ. ১০৯
লে. জেনারেল জেএফআর জ্যাকব- সারেন্ডার অ্যাট ঢাকা: একটি জাতির জন্ম, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, পৃ. ১২১
মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহম্মদ ইবরাহীম, মিশ্র কথন, অনন্যা, পৃ. ২১৬
অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী- জেনারেল ওসমানী এবং পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণ, বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৭ ডিসেম্বর ২০১৫
মেজর জেনারেল (অব.) এসএস উবান- ফ্যান্টমস অব চিটাগং: দ্য ফিফথ আর্মি ইন বাংলাদেশ। ঘাস ফুল নদী। পৃ. ১২০
১৯৫৫ সালের ১২ ডিসেম্বর পাকিস্তান সেনাসদরে মিলিটারি অপারেশন ডাইরেক্টরেটে জেনারেল স্টাফ অফিসার গ্রেড-১ হিসেবে এবং ১৯৫৬ সালের ১৬ মে কর্নেল পদে পদোন্নতি পেয়ে মিলিটারি অপারেশন ডাইরেক্টরেটে ডেপুটি ডাইরেক্টরের দায়িত্ব নিযুক্ত হন। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে তিনি বীরত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। এ সময় তিনি আন্তর্জাতিক সংস্থা সিয়াটো ও সেন্টোতে পাকিস্তান বাহিনীর প্রতিনিধিত্ব করেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত থাকাকালীন ওসমানী একজন স্পষ্টভাষী, স্বাধীনচেতা, নির্ভীক কর্মকর্তা হিসেবে পরিচিত ছিলেন এবং বাঙালি সেনাদের অধিকার রক্ষার্থে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।
পাকিস্তানি বাহিনী ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সামরিক বাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করে। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। এই আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওসমানী উপস্থিত ছিলেন না। আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে ভারতের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্ব ফ্রন্টের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট.জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা। অন্যদিকে পাকিস্তানের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় সৈন্যবাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল এএকে নিয়াজী। এরা দুজনেই ছিলেন আঞ্চলিক প্রধান।
বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করে ওসমানী তৎকালীন সেনাবাহিনীতে যোগ দেন৷ ১৯৩৯ সালে তিনি রয়্যাল আর্মড ফোর্সে ক্যাডেট হিসেবে যোগ দেন। দেরাদুনে ব্রিটিশ- ইন্ডিয়ান মিলিটারি একাডেমিতে প্রশিক্ষণ শেষে তিনি ১৯৪০ সালে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেন কমিশন্ড অফিসার হিসেবে। সেসময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিলো। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর একটি ব্যাটেলিয়ানের কমান্ডার হিসেবে তিনি বার্মা (মিয়ানমার) সেক্টরে কাজ করেন। ১৯৪২ সালে মেজর পদে উন্নীত হন। ১৯৪২ সালে ওসমানী ছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্বকনিষ্ঠ মেজর।
১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে ওসমানী ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে লং কোর্স পরীক্ষা দিয়ে উচ্চস্থান লাভ করেন৷ সে বছর তিনি ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল সার্ভিসের জন্যও মনোনীত হন৷ কিন্তু তিনি সামরিক বাহিনীতেই থেকে যান৷
দেশবিভাগের পর ১৯৪৭ সালের ৭ই অক্টোবর ওসমানী পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। এসময় তার পদমর্যাদা ছিল লেফটেন্যান্ট কর্নেলের। ১৯৪৯ সালে তিনি চিফ অফ জেনারেল স্টাফের ডেপুটি হন। ১৯৫১ সনে তিনি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এর ১ম ব্যাটেলিয়নের অধিনায়ক নিযুক্ত হন৷ এর পর তিনি চট্টগ্রাম সেনানিবাস প্রতিষ্ঠা করেন৷ ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ববাংলার আরও কয়েকটি আঞ্চলিক স্টেশনের দায়িত্বও তিনি সফলতার সাথে পালন করেন৷
জাতীয় সম্মিলিত ফোরাম পত্রিকায় প্রকাশিত একজন লেখকের সাক্ষাৎকার ও আর্টিকেল থেকে বিবৃতিতে থেকে বিবৃত করে বলেছে , পরবর্তীকালে তিনি ১৪তম পাঞ্জাব রেজিমেন্ট এর ৯ম ব্যাটেলিয়ানের রাইফেলস কোম্পানির পরিচালক, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর)-এর অতিরিক্ত কমান্ড্যান্ট, সেনাবাহিনীর জেনারেল স্টাফ অফিসার প্রভৃতি দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৬ সালে তিনি কর্নেল পদমর্যাদা লাভ করেন এবং সেনাবাহিনীর হেডকোয়ার্টারের জেনারেল স্টাফ এন্ড মিলিটারি অপারেশনের ডেপুটি ডিরেক্টরের দায়িত্ব পান। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে তিনি পাকিস্তানের হয়ে যুদ্ধ করেন৷ 'ডেপুটি ডাইরেক্টর অব মিলিটারি অপারেশন' হিসেবে যুদ্ধরত বিভিন্ন সামরিক হেডকোয়ার্টারে যোগাযোগ করতেন তিনি ৷ ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ যখন শেষ হয় তখন তার বয়স চল্লিশের উপরে৷ ১৯৬৬ সালের মে মাসে তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে অবসরকালীন ছুটি নেন এবং পরের বছর (১৯৬৭ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি) অবসর গ্রহণ করেন।
ওসমানীর নির্দেশনা অনুযায়ী সমগ্র বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। প্রতিটি সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার হিসেবে এক একজন সেনাবাহিনীর অফিসারকে নিয়োগ দেয়া হয়। বিভিন্ন সেক্টর ও বাহিনীর মাঝে সমন্বয়সাধন করা, রাজনৈতিক নেতৃত্বের সাথে যোগাযোগ রাখা, অস্ত্রের যোগান নিশ্চিত করা, গেরিলা বাহিনীর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা-প্রভৃতি কাজ সাফল্যের সাথে পালন করেন ওসমানী। ১২ এপ্রিল থেকে এমএজি ওসমানী মন্ত্রীর সমমর্যাদায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি হিসেবে যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন৷ রণনীতির কৌশল হিসেবে প্রথমেই তিনি সমগ্র বাংলাদেশকে ভৌগোলিক অবস্থা বিবেচনা করে ১১টি সেক্টরে ভাগ করে নেন এবং বিচক্ষণতার সাথে সেক্টরগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে থাকেন৷
জেনারেল ওসমানী ছিলেন অসম সাহসী এবং প্রচণ্ড স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী- মুক্তিযুদ্ধ এবং পরবর্তী সময়ে তাঁর রাজনৈতিক জীবনেও এর প্রতিফলন দেখা যায়। একাত্তরে ওসমানী ছিলেন বাংলাদেশ বাহিনীর প্রধান। কিন্তু নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের শেষে, ১৬ ডিসেম্বর বিকালে পরাজিত পাকিস্তান বাহিনী রেসকোর্সের ময়দানে যখন আত্মসমর্পণ করলো, সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে সেখানে তিনি উপস্থিত ছিলেন না। কেন তিনি অনুপস্থিত ছিলেন, তা নিয়ে পরবর্তীতে জল কম ঘোলা হয়নি! এ নিয়ে বিভিন্ন লেখকের গ্রন্থে যেসব ভাষ্য পাওয়া যায়, তা আলোচনার জন্য সহায়ক হলেও মূল প্রশ্নের সুরাহা করতে যথেষ্ট নয়। বরং অনেকের বক্তব্য এমনভাবে উপস্থাপনা করা হয়েছে, তাতে যে কারো ধারণা জন্মাতে পারে, ওসমানী হয়তো ইচ্ছে করেই আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে যাননি। অনুপস্থিত থাকার দায় অত্যন্ত কৌশলে তাঁর ওপরে চাপানোর চেষ্টা করা হয়। এভাবে তাঁর ব্যক্তিত্বকেও খাটো করা হয়েছে, হচ্ছে। ওসমানীর জীবনের সফলতা-ব্যর্থতার মধ্যে এ অধ্যায়টিই সবচেয়ে বেশি আলোচিত। বর্তমান নিবন্ধেও এই বিষয়টিকে মূল ‘ফোকাস’করে পরস্পরবিরোধী সেসব বক্তব্যের বিশ্লেষণ তুলে ধরার চেষ্টা থাকবে।
তথ্য সূত্র: এ কে খন্দকার, মাঈদুল ইসলাম ও এস আর মীর্জা- মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর কথোপকথন। প্রথমা প্রকাশন। পৃ. ৯৮
জাফরুল্লাহ চৌধুরী- মুক্তিযুদ্ধের কয়েকটি খণ্ড চিত্র, নতুন দিগন্ত, ষোড়শ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা এপ্রিল-জুন ২০১৮, পৃ. ৫৭ থেকে ৫৯
অলি আহাদ- জাতীয় রাজনীতি: ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড, পৃ. ৪৩৩
মহিউদ্দিন আহমদ- আওয়ামী লীগ: যুদ্ধদিনের কথা ১৯৭১। প্রথমা প্রকাশন, পৃ. ১৪৬
ফারুক আজিজ খান- বসন্ত ১৯৭১। প্রথমা প্রকাশন। পৃ. ১৯৩
জাতীয় সম্মিলিত ফোরাম (জেএসএফ ) বিবৃতিতে বলেছে , বিভিন্ন ধরনের ভাষ্য পাওয়া যায়। যুদ্ধের একটা পর্যায়ে ওসমানীকে ঘিরে কড়া নজরদারি করা হতো, সব ধরনের দায়িত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছিল, তাঁকে যুদ্ধের ময়দানেও যেতে দেয়া হতো না। ওসমানীর জন্য এই পরিস্থিতি ছিল বিব্রতকর এবং অপমানজনক। তারপরও ভারতের এবং প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের অনেক সিদ্ধান্তের জোরালো প্রতিবাদ করতেন তিনি, তেমন দৃষ্টান্তও আছে। মুক্তিযোদ্ধা ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী লক্ষ্ণৌতে গিয়েছিলেন চিকিৎসাধীন সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফকে দেখতে। কলকাতায় ফেরার পথে বিমানে আবদুস সামাদ আজাদের সঙ্গে তার দেখা হয়। তিনি দিল্লি থেকে কলকাতায় ফিরছিলেন। আবদুস সামাদ আজাদ তাদের দু’জনের দেখা হওয়ার বিষয়টি জাফরুল্লাহকে গোপন রাখতে বলেন। এতে জাফরুল্লাহ’র সন্দেহ হয়। তিনি সামাদ আজাদের কাছে জানতে চান- ‘দিল্লিতে কী করলেন? কোনো চুক্তি হয়েছে কি?’ এরপর বিমানে বসে তাদের দু’জনের মধ্যে যে আলোচনা হয় সামাদ আজাদের নিষেধ অগ্রাহ্য করে কলকাতায় ফিরে এসে ওসমানীকে সব বলে দেন জাফরুল্লাহ। শুনে ক্ষুব্ধ হন ওসমানী। এরপর যা ঘটেছিল, জাফরুল্লাহ’র ভাষায়- ‘‘ওসমানী সাহেব সোজা প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন সাহেবের ঘরে ঢুকে উচ্চস্বরে কথা বললেন, ‘You sold the country. I will not be a party to it.’ তাজউদ্দিন সাহেব ওসমানীকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন, নিচু স্বরে কী বললেন আমি শুনতে পেলাম না। আমি দরজার বাইরে ছিলাম।’’
কলকাতায় ফিরে জেনারেল ওসমানীকে কী বলেছিলেন জাফরুল্লাহ, তা তিনি পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা দেননি। তবে ধারণা করা হয়, তাজউদ্দিনের ওপরে ওসমানীর সেদিনের ক্ষোভের কারণ ছিল দু’দেশের মধ্যে সম্পাদিত সাত দফা চুক্তি, যা ছিল গোপনীয়। যুদ্ধ চলাকালে সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের ২/৪ জন অবগত থাকলেও ভারতে আশ্রিত বেশির ভাগ বাংলাদেশির কাছে এই চুক্তির বিষয়টি ছিল অজানা। ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে ভারত সরকারের সঙ্গে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার প্রশাসনিক, সামরিক, বাণিজ্যিক, পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা বিষয়ে একটি সাত দফা গোপন সমঝোতা চুক্তি সম্পাদন করে (তথ্যসূত্র: জাতীয় রাজনীতি: ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫- অলি আহাদ)
সাত দফা চুক্তির কারণেই সম্ভবত জেনারেল ওসমানী সেদিন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনের বিরুদ্ধে ‘দেশ বিক্রি’র অভিযোগ করেছিলেন এবং ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। জাফরুল্লাহ চৌধুরীর বর্ণনায় তার মিল খুঁজে পাওয়া যায়, ‘‘কয়েকদিন পর উভয়ের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয় ভারতীয় একটি প্রস্তাবনা নিয়ে। ডিসেম্বরে দেশ স্বাধীন হলে আইন-শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য বেশ কয়েকজন বাঙালি প্রশাসনিক ও পুলিশ অফিসাররা বাংলাদেশের সব বড় শহরে নির্দিষ্ট মেয়াদে অবস্থান নেবেন। ওসমানী সাহেব বললেন, ‘এটা হতে পারে না, আমাদের বহু বাঙালি অফিসার আছেন। কেউ কেউ পাকিস্তানে আটকা পড়েছেন। তারা নিশ্চয়ই ফিরে আসবেন।’ ওসমানী সাহেবের সঙ্গে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রীদের মতপার্থক্যের কথা জেনে ভারতীয়রা আরও সতর্ক হলেন। ওসমানী সাহেবকে তারা কড়া নজরে রাখলেন। কাগজে-কলমে যৌথ কমান্ডের কথা থাকলেও বস্তুত তাঁরা ওসমানী সাহেবকে একাকী করে দিলেন। ভারতীয়রা সব কমান্ড নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করলেন। ওসমানী সাহেবের সঙ্গে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সম্পর্কের দ্রুত অবনতি ঘটলো।’’
জেনারেল ওসমানীকে হত্যার জন্য ভারতের রয়ের সাথে চক্রান্ত করেছিল কারা ?
তথ্য সূত্র: রাও ফরমান আলী খান- বাংলাদেশের জন্ম। দি ইউনিভার্সিটি লিমিটেড। পৃ. ১২.
লে. জেনারেল গুল হাসান খান- পাকিস্তান যখন ভাঙলো। দি ইউনিভার্সিটি লিমিটেড। পৃ. ৩০.
লে. জে. (অব.) কামাল মতিনউদ্দিন- ট্র্যাজেডি অব এররস্: পূর্ব পাকিস্তান সংকট ১৯৬৮-১৯৭১, পৃ. ১৭৪
লে. কর্নেল (অব) এমএ হামিদ- তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা। মোহনা প্রকাশনী। পৃ. ৮৬-৮৭
এ কে খন্দকার- ১৯৭১: ভেতরে-বাইরে। প্রথমা প্রকাশন। পৃ. ২০৭
জেএসএফ বিবৃতিতে বলেছে , যুদ্ধজয়ের আগ মুহূর্তে ‘ওসমানী কোথায় ছিলেন’, ‘তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি’- এ ধরনের বক্তব্য সত্যকে আড়াল করার চেষ্টা ছাড়া কিছু নয়। যারা এ ধরনের বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়েছিলেন, তাদের একজন ছিলেন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের কর্মকর্তা রুহুল কুদ্দুস। বাংলাদেশ পুলিশের সাবেক আইজি ও স্বরাষ্ট্র সচিব আবদুল খালেকের এক বর্ণনায় এমন তথ্য পাওয়া যায়। ১৯৭১ সালে আবদুল খালেক ছিলেন সারদা পুলিশ অ্যাকাডেমির অধ্যক্ষ। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি ভারতে গিয়ে মুজিবনগর সরকারে যোগ দেন। তিনি লিখেছেন, ‘‘বিজয় যখন দিবালোকের মতো স্পষ্ট, তখন আত্মসমর্পণ উৎসবে আমাদের যোগদান সম্পর্কে যে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়, তাতে স্থির করা হয়েছিল ১৬ ডিসেম্বর কর্নেল ওসমানী, রুহুল কুদ্দুস ও আমি হেলিকপ্টারে ভারতীয় কমান্ডারকে নিয়ে ঢাকায় পৗঁছাবো। দমদম এয়ারপোর্টে পৌঁছার জন্য যে সময় দেয়া হয়েছিল, তার ঘণ্টাখানেক আগে আমাদের প্রশাসনে কী যেন একটি হাশ হাশ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। আমি তার কিছুই আঁচ করতে পারিনি। রুহুল কুদ্দুস শুধু জানালেন যে, ‘কর্নেল ওসমানীকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।’ কাজেই ডেপুটি কমান্ডার ইন চিফ একে খন্দকারকে খুঁজে বের করা হয়েছে। শুধু তিনি ঢাকায় যাবেন। আমরা দু’জন যাবো না। কর্নেল ওসমানীর সঙ্গে কার কী মতভেদ ঘটেছিল তা আর জানতে পারিনি।’’
ওসমানী যে সিলেটের মুক্তাঞ্চল পরিদর্শনে গিয়েছিলেন সেটা এ কে খন্দকারের জানা ছিল। তিনি ছিলেন বাংলাদেশ বাহিনীর উপপ্রধান। ওসমানীর অবস্থান সম্পর্কে তিনি অবগত থাকা মানে প্রধানমন্ত্রী এবং প্রবাসী সরকারেরও বিষয়টি অজানা থাকার কথা নয়। তাছাড়া, জাফরুল্লাহ’র বক্তব্যে ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি, ওসমানী কোথায় যাচ্ছেন, কী করছেন, তা কড়া নজরদারি হতো।
ওসমানীর সেদিনের সফরসঙ্গী ও ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর বর্ণনা থেকে বিষয়টির আরও পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন- ‘‘ভারতীয় এম-৮ হেলিকপ্টারে সিলেটের পথে চলেছি। ...অতর্কিতে একটি প্লেন এসে চক্কর দিয়ে গেল। হঠাৎ গোলা বিস্ফোরণের আওয়াজ, ভেতরে জেনারেল রবের আর্তনাদ। পাইলট চিৎকার করে বলল, ‘উই হ্যাভ বিন অ্যাটাকড। ...অয়েল ট্যাংক হিট হয়েছে। তেল বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি বড়জোর ১০ মিনিট উড়তে পারবো।’ ...ওসমানী লাফ দিয়ে উঠে অয়েল ট্যাংকারের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করলেন, ‘জাফরুল্লাহ, গিভ মি ইউর জ্যাকেট’। আমি আমার জ্যাকেট ছুড়ে দিলে, ওসমানী সাহেব সেটা দিয়ে তৈলাধারের ছিদ্র বন্ধের চেষ্টা করতে থাকলেন। ...কার গোলাতে এই দুর্ঘটনা? পাকিস্তানের সব বিমান তো কয়েকদিন আগেই ধ্বংস হয়েছে, কিংবা গ্রাউন্ডেড করা হয়েছে। তাহলে আক্রমণকারী বিমানটি কাদের? গোলা ছুড়ে সেটি কোথায় চলে গেল? ...ওসমানী নিচে একটা জায়গার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, ‘ল্যান্ড হেয়ার’।...লাফ দিয়ে তিনি নামলেন। ...সঙ্গে নামলাম নিজেও। আমার পেছনে পেছনে অন্যরা লাফিয়ে নামলেন। হেলিকপ্টারটা আমাদের চোখের সামনে দাউ দাউ আগুনে পুড়ছে।’’
প্রসঙ্গত, ওই হেলিকপ্টারটিতে যাত্রী ছিলেন মোট আটজন- জেনারেল ওসমানী, তাঁর এডিসি শেখ কামাল, মুক্তিবাহিনীর চিফ অব স্টাফ জেনারেল এমএ রব, সাংবাদিক আল্লামা, ব্রিগেডিয়ার গুপ্ত, ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী এবং ভারতীয় দুই পাইলট। অজ্ঞাত বিমানের গোলার আঘাতে বিপর্যস্ত হেলিকপ্টারটি মাটিতে নামার পর আগুনে পুড়ে গেলেও এর যাত্রীরা সবাই প্রাণে বেঁচে যান।খবর বাপসনিউজ ।
১৯৮৪ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি মহান জননেতা বঙ্গবীর জেনারেল এম এ জি ওসমানী লন্ডনের সেন্টপল হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। ২০ ফেব্রুয়ারি পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাকে তার অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী হজরত শাহজালাল রহ:-এর দরগা শরিফসংলগ্ন তার মায়ের কবরের পাশে সমাহিত করা হয়।
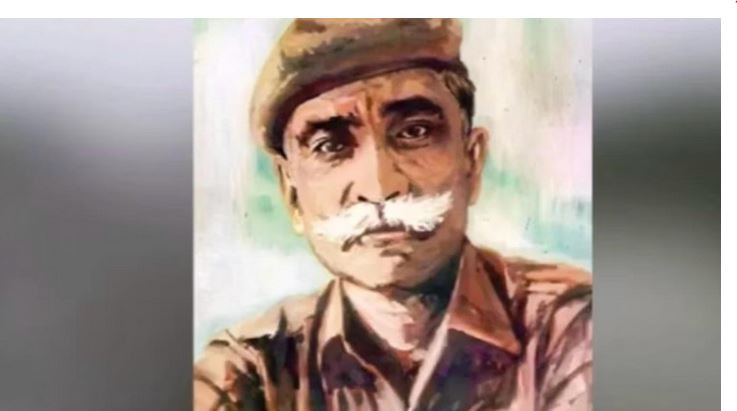








মন্তব্যসমূহ (০) কমেন্ট করতে ক্লিক করুন